কবিতার কাজ যদি হয় ভাষা দিয়ে এমন এক বাস্তব নির্মাণ করা, যা পাঠকের চৈতন্যকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়, তবে সব্যসাচী মজুমদার নিশ্চিতভাবেই এক আধুনিক কবিতার কারিগর। তাঁর কবিতা পঠনের অভিজ্ঞতা একান্তই শরীরগত, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক দ্বন্দ্বে ঘেরা এক ভ্রমণ, যা পাঠককে সরলীকরণের বিপরীতে ঠেলে দেয়। এখানে কবিতা খণ্ড নয়, বরং প্রবাহ। এক ধরনের ভাষিক-সমগ্র যার মধ্যে ‘অংশভাগ’ হয়ে থাকে শরীর, মন, সমাজ, প্রকৃতি এমনকি ভাঙা ইতিহাসও।
সব্যসাচী মজুমদারের কবিতা এক অভিযান, যেখানে ভাষা শুধু বাহন নয়, বরং অন্বেষণের ক্ষেত্র; তাঁর পংক্তিমালা এক একটি জৈব-ভূখণ্ডের মতো বিচ্ছিন্ন, অথচ অভ্যন্তরীণ ছন্দে সংযুক্ত। তাঁর কবিতায় সময়, দেহ, ভাষা, যৌনতা ও ভূগোলের রক্তমাখা উপস্থিতি যেমন আছে, তেমনি আছে একধরনের জৈবিক নিরুদ্দেশতা—যা নিতান্ত চেনা বাস্তবের বাইরে, অথচ তারই অংশ। তাঁর কবিতা কোনো একক ব্যক্তিসত্তা ধারণ করে না—বরং ছড়িয়ে থাকে অনেক স্তরে।
এই স্তরবিন্যাসের একটি দৃষ্টান্ত হল “অংশভাগ” কবিতাটি, যা বারোটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এক বিরাট অনুভূতির অনুপুঙ্খ পাঠ তৈরি করে। কবিতার প্রথম অংশেই উচ্চারণ করা হয় এক আত্মগত প্রত্যাহার, যে প্রত্যাহার কোনো আত্মদংশ নয়, কিংবা নিছক আত্মবিমুখতা নয়, বরং ইতিহাস, প্রেম ও সময়ের সামনে দাঁড়িয়ে এক ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনর্জন্মের ইঙ্গিত। “পিছিয়ে এসেছি যত, ততটাই তোমার রোদ্দুর / যত দীর্ঘকাল যাই ততই শকুন…”—এই দুই পংক্তি যেন কবিতার গোড়াতেই পাঠককে জানান দেয়, এখানে সময় রৈখিক নয়; বরং ছিন্ন অংশের সমাহার। রোদ্দুর ও শকুনের দ্বৈততা আমাদের বুঝিয়ে দেয়, আলো ও মৃতদেহ একই পৃথিবীর বাসিন্দা। এই দ্বৈততাই সব্যসাচীর কবিতার কেন্দ্রে অবস্থিত।
এই দ্বৈততার সঙ্গে যুক্ত হয় ফসিল, বাঁশি ও লিপির প্রসঙ্গ, যা একরকম প্রত্নচেতনাকে হাজির করে। “আমি কি বুঝি না তার বাঁশি, তার লিপি ও ফসিল”—এই পংক্তিতে ভাষা, সংগীত ও ইতিহাসের সংমিশ্রণে গঠিত এক পাণ্ডুলিপির আভাস পাওয়া যায়। কবি এক অতীত-অভিজ্ঞ অনুসন্ধানী, যে বসন্তকালেও সামুদ্রিক প্রাণীর জন্ম প্রত্যক্ষ করে এবং এইসব বেঁচে উঠতে চাওয়া প্রাণী দেখে “বিশ্বাস করে মমির বিদ্বেষ”। বিদ্বেষ এখানে ভয় কিংবা অস্বীকার নয়, বরং মৃতকে শত্রু বলে মানার মধ্যে দিয়ে জীবনের প্রামাণ্যতা পুনরুদ্ধার।
এই দ্বন্দ্বে ধরা পড়ে শরীর ও দেহের ভেতরকার দূরত্ব। “যদিও দেহটি শরীরের মতো নয় / দ্রবণ দ্রবণ যুগ পার…”—এই উচ্চারণে সময়ের সঙ্গে শরীরের বিকলতা এক হয়ে যায়। শরীর আর প্রমাণ নয়, বরং দ্রবণে দ্রবণে ভেসে যাওয়া এক অবয়ব। এই দ্রবণের সঙ্গে যুক্ত হয় শরণার্থীত্ব—“নদী ডাকতে এখনও পার না / তুমি কি গো! / বস্তুত শরনার্থী প্রবাহ!” শরীর হয়ে ওঠে বহিষ্কৃত, অসার, অথচ প্রবাহমান। এই ‘নদী না ডাকার’ অপারগতা প্রেমেরও, সময়েরও।
একইসাথে দেখা যায়, বাষ্প, রোদ্দুর ও শ্রেণি-জটিলতার এক চমৎকার ব্যবচ্ছেদ। “বাষ্পের ভূমিকা বুঝি / কীভাবে জটিল হয় তার শ্রেণি!” এই শ্রেণিবিন্যাস শুধু সামাজিক নয়, প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যেও এক ক্ষমতার পরিসর নির্মাণ করে। সেই পরিসরে “একটি রোদ হয়ে গেছিল আরেক রোদ”—একটি আলোর অস্তিত্বকে গ্রাস করে অন্যটি। এই স্বপ্লবাক্য রচনার মধ্য দিয়ে সব্যসাচী ভাষার প্রপঞ্চটিকে উন্মোচন করেন, যেখানে ফাল্গুন এসে “কেবল বাগার্থ ঘটে”। সে ভাষা আর নিছক যোগাযোগ নয়, বরং এক ধরণের ছদ্মভাবনার উৎপত্তিস্থল।
কবিতায় কখনো কখনো ‘তুমি’ হয়ে ওঠে কৃষিজীবী, সংসারী অথবা প্রাকৃতিক প্রাচীনতায় গড়া এক শরীর। “তুমি ক্ষেতে ক্ষেতে পটল বুনেছ / পটলের ওপরে ওস / তাতে তৃতীয় দুনিয়া…”—এই পংক্তি কৌতুকমিশ্রিত হলেও প্রহসনের আড়ালে সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতা অনুপমভাবে ধরা পড়ে। পটল শুধুই সবজি নয়; এটি হয়ে ওঠে তৃতীয় বিশ্বের প্রতীক—যার উপর অপ্রত্যাশিতভাবে ওস পড়ে, হয়তো আন্তর্জাতিক দৃষ্টি বা সাম্রাজ্যিক হস্তক্ষেপ। এই অনুপুঙ্খের মাধ্যমে সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতি এক অন্তঃস্রোতের মতো কবিতায় ঢুকে পড়ে।
শরীর ও সমাজের দ্বিমুখিতা আরও সুস্পষ্ট হয় “তুমি দ্বিমুখী হরিণ / দৌড়ে পার হচ্ছ সন্ন্যাস-গ্রহণ, কিসসা, রামায়ণ” উচ্চারণে। এখানে হরিণ শুধু নিরীহ নয়; ছলনারও আরেক নাম, দ্বিধাগ্রস্ত এবং ধর্মীয় আখ্যানের সীমায় ধাবমান। এই দ্বিমুখীতা বাঙলা আধুনিক কবিতায় বহুল ব্যবহৃত হলেও সব্যসাচীর হাতে তা মিথ-উন্মোচনকারীর মতো হয়ে ওঠে—যেখানে ‘সিউডো ধারণা’ মাথায় নিয়েই প্রেম, সমাজ ও ইতিহাস ছুটে চলে।
সবচেয়ে সংবেদনশীল ও দর্শনমূলক যে অনুচ্ছেদটি দেখা যায় তা হল—“কিছুটা পাহাড়ি ছাঁদে আমার মরণ / সেভাবে কি বলা যায়— কেন যে মরেছি!” এখানে মৃত্যু ব্যক্তিগত নয়; তা এক অভিজ্ঞতার ভাষায় রূপান্তরিত হয়। সেই মৃত্যু রেণুতে পৌঁছায়, পূণর্ভবার প্রশ্ন তোলে। অথচ কবি স্বীকার করেন: “বুঝিনি আমি তোমার হলুদ / বুঝিনি তোমার মতো ওড়ার কারণ”। এই ‘তোমার’ প্রতীক কখনও নারী, কখনও দেশ, কখনও স্বপ্ন—তবে তার মূল রহস্য এক অপার ওড়ার ভঙ্গিমা।
শেষদিকে এসে কবি আমাদের ফেলে যান একটি স্তম্ভিত বাস্তবতার মুখোমুখি। “তবে কি অবর্ণনীয় ঘাসে / আমি হাড় কটি পুঁতে চলে যাব?”—এই প্রশ্নে মৃত্তিকার সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হয়। এই হাড় পোঁতা এক মুদ্রাদোষ নয়; বরং তা নতুন ভাষার জন্মস্থান। কারণ পরক্ষণেই উচ্চারিত হয়: “তুমি দেখবে অবিন্যস্ত ভূমি / ফুটেছে জগৎ…”—এ যেন মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এক জগৎ তৈরি হবার রহস্য।
এই রহস্যের অভ্যন্তরে থাকে এক বিক্ষিপ্ত গান, এক ভাঙা নদীর পার হয়ে যাওয়া, একক শেয়ালের ডাক, এবং প্রান্তিক জনতার কোলাহল—যা সব্যসাচীর কাব্যভাষায় গড়ে তোলে এক প্রত্নঋতু। এই কবিতাগুলো পাঠক ফিরে ফিরে পড়ে; পড়তে হয়। কারণ এগুলো এক পাঠে আত্মস্থ হয় না, বরং শরীরের ভেতরে জমে থাকে।
শুধু “অংশভাগ” নয়, “কবিতা”, “যৌথরাগ” ও “সারঙ”-এর মতো কবিতাগুলিও সেই জৈবিক-বিকল চৈতন্যের ধারক। “কবিতা”-য় লেখা হয়, “একাকী মাংসের বিনীত চলে যাওয়া / তুমুল মেঘ দিল অসহ্যে…”—এ যেন আত্মার মাংসে রচিত বেদনা। আবার “যৌথরাগ”–এ যৌনতা এক চৈতন্য হয়ে ওঠে। সেখানে বলা হয়: “দ্রংষ্ট্রা চাই লিঙ্গ চাই / নিঃসহায় তক্ষকের / গন্ধ চাই স্বপ্ন চাই”—যৌনতা এখানে পুরুষতন্ত্রের ভাষায় নয়, বরং এক আকুল প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ায় রূপান্তরিত।
“সারঙ” কবিতায় আবার নদী ও শরীর এক অনুপম মিথোজীবিতার ভাষা রচনা করে—“তুমি তা জেনেও ফের রুক্ষস্তনদ্বয় / মেলেছো রোদের দিকে মফসসলি মেয়ে”—এই মফস্বল যেন শুধু ভৌগোলিক নয়, এক সাংস্কৃতিক উপনিবেশ, যেখানে নারী শরীর বারবার ধুয়ে নেয় প্রান্তিকতা, প্রলয় ও প্রেম।
এই সবকিছু মিলে সব্যসাচীর কবিতার ভাষা হয়ে ওঠে স্বরলিপিহীন সংগীত, যার ধ্বনি শোনা যায়, অর্থ ধরা যায় না—তবে অনুভব করা যায় অক্ষরের শরীর। তাঁর কবিতা কেবল পাঠ্য নয়, এক ধরণের বহুমাত্রিক ভাস্কর্য, যাকে ছুঁতে গেলে আপন শরীরের সীমা টের পাওয়া যায়।
[দ্রষ্টব্য: আলোচ্য কবিতাগুলো লিটল ম্যাগাজিন ‘বিন্দু’ থেকে নেয়া হয়েছে৷]

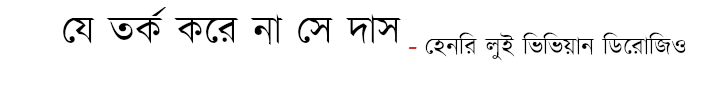









16 মন্তব্যসমূহ
যথাযথ বিশ্লেষণ। লেখক যখন কবিতার ভাব তার প্রকাশ কবির লেখনিকে আশ্রয় করে সমুদ্র সাঁতরে গভীরে মুক্ত তুলে আনলেন এবং তা পাঠকের কাছে উপস্থিত করলেন। তা সত্যি লেখক ও কবি দুজনকেই উদ্ভাসিত করে সমগ্র মননশীল পাঠকের কাছে। আর এখানেই এ লেখনির সার্থকতা।🌹👍
উত্তরমুছুনসাম্য রাইয়ানের প্রবন্ধ শ্বেতপত্রের সেরা প্রাপ্তি৷ মোখলেছুর সম্পাদক ধন্য৷ সাম্যের মতো গুণী লেখক এত মূল্যবান প্রবন্ধ দিয়েছে ওকে৷ লেখাটি অমর হয়ে থাকবে৷
উত্তরমুছুনপড়লাম ওস্তাদ ৷ সেরা ৷৷
উত্তরমুছুনজন্মদিনে দূর দেশ থেকে সাম্যর মতো অভিজ্ঞ পাঠকের পাঠপ্রতিক্রিয়া — এমন প্রাপ্তি ঈর্ষার জন্ম দেয়…
উত্তরমুছুনসাম্য রাইয়ানের কলমে উঠতে পারা মানেই অনন্য প্রাপ্তি৷ অভিনন্দন সব্য
উত্তরমুছুনখুব সুন্দর আলোচনা একজন সুযোগ্য মানুষের লেখা নিয়ে।
উত্তরমুছুনসুন্দর আলোচনা। শুভকামনা
উত্তরমুছুনশুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সাহিত্য যখন বিনোদন শুধু নয় ভাবনা ও মননের বিষয়ে হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে তখন তা সার্থক সাহিত্য হয়ে ওঠে। আর এখানেই সাম্য আপনি যথাযথ।🌹👍
উত্তরমুছুন"...সব্যসাচী মজুমদার নিশ্চিতভাবেই এক আধুনিক কবিতার কারিগর.........." এই বক্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ সহমত..জন্মদিনে কবিকে শুভেচ্ছা জানাই..
উত্তরমুছুনএকদম যথাযথ। কবির কলমের গভীরতার যথার্থ বিশ্লেষণ আমাদের ও মুগ্ধ করেছে। জন্মদিনের প্রাণভরা শুভেচ্ছা জানাই।
উত্তরমুছুনসার্বিক মূল্যায়ন...
উত্তরমুছুনঅভিনন্দন সাম্য রাইয়ান
শুভেচ্ছা Sabyasachi Majumder
মরমী পাঠকের আলো ফেলা 🍀
উত্তরমুছুনঅমূল্য এ লেখা
অনেকদিন পর কবিতা নিয়ে এরকম বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ পড়লাম৷ ধন্যবাদ লেখককে
উত্তরমুছুনচমৎকার বিশ্লেষণ হইসে সাম্যদা
উত্তরমুছুনসব্যসাচীর কবিতা পড়িনি৷ আপনার আলোচনা পড়ে বুঝলাম কী রত্ন মিস করেছি এতদিন৷
উত্তরমুছুনএকজন কবির কবিতা নিয়ে এমন চমৎকার আলোচনা সচারাচর দেখি না।
উত্তরমুছুনসত্যিই মনোমুগ্ধকর সাম্য' দা। মুগ্ধ হলাম।
অমার্জিত মন্তব্য করে কোনো মন্তব্যকারী আইনী জটিলতায় পড়লে তার দায় সম্পাদকের না৷